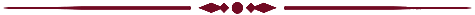
প্রথম যখন ইউরোপে যাই, অনেক-কিছু, দেখেই তখন ভারী অবাক হয়েছিলাম। রাস্তাঘাট তকতকে পরিষ্কার, জঞ্জালের ডাঁই তো দূরের কথা, কোথাও এক-টুকরো ছোঁড়া কাগজ কি আধপোড়া সিগারেটও পড়ে থাকতে দেখিনি। দোকানপাটও ঝকঝকে। তাছাড়া সেখানে বিকিকিনির ব্যাপারটাও চলছে অতি সুশৃঙ্খলভাবে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় কিন্তু, কম নয়, ফুটপাথেও প্রচুর মানুষ। কিন্তু না আছে যানবাহনের কান-ফাটানো হর্নের আওয়াজ, না হকার আর পথচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচি। দেখে সত্যিই তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। সবচেয়ে তাজ্জব হয়েছিলাম এইটে দেখে যে, যাঁরা মস্ত-মস্ত ট্রাক, ডেলিভারি ভ্যান কি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই পুরুষ নন, মহিলা। এ হল চল্লিশ বছর আগের কথা। মেয়েরা ট্রাক, ভ্যান কি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, প্রাচ্য পৃথিবীর এই এলাকায় এটা তখন কল্পনাও করা যেত না।
এখন কিন্তু যায়। সত্যের খাতিরে কবুল করব, হেভি ভিহিকল বা ভারী গাড়ির স্টিয়ারিং-হুইল এখনও পর্যন্ত কোনও মহিলার হাতে আমি এ-দেশে দেখিনি বটে, তবে দু'চার বছরের মধ্যে তাও হয়তো চোখে পড়বে। কথাটা এইজন্যে বলছি যে, এককালে যে-সব কাজকে 'পুরুষদের কাজ' বলে গণ্য করা হতো, তার অনেকগুলিকেই মহিলারা ইতিমধ্যে স্বচ্ছন্দে তাঁদের হাতে তুলে নিয়েছেন এবং অক্লেশে প্রমাণ করেছেন যে, সুযোগ পেলে সে-সব কাজ পুরষদের তুলনায় তাঁরাও কিছু কম নিপুণভাবে করতে পারেন না। শিক্ষকতা, সেবিকাবৃত্তি ও এইরকমের আরও গুটিকয়েক কাজের বাইরে এ-দেশের মেয়েদের এককালে পা বাড়াতে দেখিনি। এখন কিন্তু সেই লক্ষণের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের কর্মজীবনের বৃত্ত এখন অনেক বড়। বৃহৎ নানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার থেকে বিমান-চালনা, কোনও কাজেই তাঁরা পিছিয়ে নেই। ঝক্কি-ঝামেলার অসংখ্য কাজের দায়িত্ব তাঁরা সহজেই সামলাচ্ছেন।
আসলে এত সব কথা উঠতই না, যদি না হঠাৎ গত বছর একদিন খবরের কাগজ খুলে হরেক রকমের খবর পড়তে-পড়তে হঠাৎ ছোট্ট একটি খবরের উপরে আমাদের চোখ আটকে যেত। খবরটা আর কিছুই নয়, কলকাতার 'মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর সমাবর্তন উৎসবের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট অঞ্চলের মধ্যে এটিই হচ্ছে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার একমাত্র কলেজ। তবে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কেন, আফ্রিকারও নানা দেশের ছাত্র এখানে আসেন এই বিদ্যায় পারঙ্গম হবার জন্যে। যেমন ইথিওপিয়ার ৪ জন ছাত্রও এই কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছেন। সেটাও অবশ্য বড় খবর নয়। বড় খবর এই যে, গত ৪৭ বছরে এই কলেজে ভর্তি হয়ে যাঁরা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং শিখেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন ছাত্র। মাত্র গত বছরই একজন ছাত্রী এখানে ভর্তি হয়েছেন। সমাবর্তন উৎসবে এই খবরটা সেদিন খুব আনন্দের সঙ্গে জানানো হল।
ছাত্রীটি যে বাঙালি, এটা অবশ্য আমাদের কাছে দ্বিগুণ আনন্দের খবর। ছাত্রাবাসে মহিলা-ক্যাডেটের থাকার অসুবিধে, তাই সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ এই ছাত্রীটি আপাতত স্টাফ-কোয়াটার্সে থেকেই চালাবেন তাঁর পড়াশুনো। আপাতত মানে যতদিন না আলাদা একটি ছাত্রী-নিবাস সেখানে গড়ে ওঠে। তবে, অচিরে তাও গড়ে উঠবে নিশ্চয়। কেননা, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দরজাও যখন মেয়েদের কাছে খুলে গেল, তখন আরও ছাত্রী এই বৃত্তি শেখার জন্যে ওখানে আসতে শুরু করবেন, তাতে আর সন্দেহ কী। সোনালি যে তাঁর সহপাঠী ছাত্রদের কাছ থেকে পুরো সহযোগিতা পাচ্ছেন, এটাও তো মস্ত সুখবর।
না, কোনও ক্ষেত্রেই মেয়েরা আর পিছিয়ে থাকবেন না। পিছিয়ে তাঁদের রাখা হবেই বা কেন। যে সমাজে মেয়েদের পিছিয়ে রাখা হয়, সেই সমাজই এক-পায়ে চলতে-চলতে পিছিয়ে পড়ে যে! তাই না? আপনারা কী বলেন?
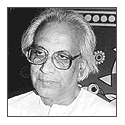
* অপ্রকাশিত এই নিবন্ধটি ১৯৯৮ সালে (বাংলা ১৪০৫ সন) লেখা।
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ শ্রী কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী।