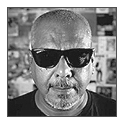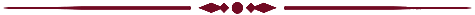
।। ৯ ।।
আঠারো শতকের আরেক কবি রামপ্রসাদ সেন, ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার পথ প্রসারিত হয়। জীবিকার জন্য তিনি উত্তর কলকাতার গরানহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করতেন।
মনে ভাবের উদয় হলে তিনি নির্জনে একা বসে গান গাইতেন; কখনও নতুন গান মনে এলে বিষয়-উদাসীন রামপ্রসাদ জমিদারির হিসাবের খাতায়ই তা লিখে রাখতেন। জমিদার রামপ্রসাদের এই ভক্তিভাব ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে এ কাজ থেকে মুক্তি দেন। তিনি রামপ্রসাদের জন্য মাসিক তিন টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন এবং শক্তিসাধনা ও সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন।
সেকালের বৈষ্ণবদর্শন-কেন্দ্রিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক কীর্তনের পাশাপাশি রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলি তথা শ্যামাসঙ্গীত সাধনসঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়ে মাতৃরূপে শক্তিসাধনার এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি ভক্তিভাব এবং রাগ ও বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন সুরের সৃষ্টি করেন, যা বাংলা সঙ্গীতজগতে 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। এই সুর পরবর্তীকালের প্রায় সকল সঙ্গীতকারকেই কম-বেশি প্রভাবিত করেছে; এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই সুরে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ নিজে এই সুরে কালী বা শ্যামার উদ্দেশে অনেক সঙ্গীত রচনা করেন, যা শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে তিনি বাংলা গানের জগতে অমর হয়ে আছেন। তিনি তাঁর গানে প্রচলিত প্রাচীন সুরের পাশাপাশি রাগসুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।
সংসারের অভাব-অনটনের বাস্তবতার মধ্যে অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েও রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী হননি। তাই সংসারের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টকে গৌরব মনে করে মায়ের উদ্দেশে তিনি গান বেঁধেছেন।
তাঁর গানের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি রামপ্রসাদকে সভাকবি হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যিনি সাধক তিনি সভাকবি হতে চাননি। তাই তিনি প্রস্তাবটি সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তাঁর সময়নিরিখে মনে হয়েছিল, রামপ্রসাদই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদ সেনের জীবন এবং সাহিত্যও বাংলার কাউন্টারকালচারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
রামপ্রসাদের একটি গানে আমরা দেশীয় পদ্ধতিতে মদ তৈরির উল্লেখ পাই। যা তখন গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অঙ্গ ছিল, এর উল্লেখ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইতেও আছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা বাংলার বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয় ভাবে মদ তৈরির এই বৈচিত্রময় লোকসংস্কৃতির এই ধারাটিকে বিলিতি কোম্পানি গঠনের আগ্রাসনে ধ্বংস করে দিয়েছে, তৈরি করেছে দিশি ও বিলিতি মদ তৈরির কোম্পানি। যে ভাবে একদিন তারা বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস করেছিল। রামপ্রসাদের গানটি হল -
সুরা পান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে মদ মাতালে মাতাল বলে।।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞানশুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি পান করে মোর মন মাতালে।।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
রামপ্রসাদ বলে, এমন সুরা খেলে চতুবর্গ মেলে।।
।। ১০ ।।
উনিশ শতকের বটতলা সাহিত্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বটতলা উ সাহিত্য ছিল মেনস্ট্রিম সাহিত্যের উল্টোদিকে বয়ে চলা কাউন্টারকালচার সাহিত্য। যার বিষয় ছিল কলকাতা তথা বাংলার ডার্ক, আন্ডারগ্রাউন্ড, আন্ডারবেলি লিটারেচার। সুকুমার সেন তাঁর 'বটতলার বই' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন -
"সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বছরেরও বেশি কাল আগে শোভাবাজার কালাখানা অঞ্চলে একটা বড় বনস্পতি ছিল। সেই বটগাছের শানবাঁধানো তলায় তখনকার পুরবাসীদের অনেক কাজ চলত। বসে বিশ্রাম নেওয়া হত। আড্ডা দেওয়া হত। গানবাজনা হত। বইয়ের পসরাও বসত। অনুমান হয় এই বই ছিল বিশ্বনাথ দেবের ছাপা, ইনিই বটতলা অঞ্চলে এবং সেকালের উত্তর কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা খুলেছিলেন, বহুকাল পর্যন্ত এই 'বান্ধা বটতলা' উত্তর কলকাতায় পুস্তক প্রকাশকদের ঠিকানা চালু ছিল... ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য ছোট সস্তার প্রেস গড়ে ওঠে। এগুলির চৌহদ্দি ছিল দক্ষিণে বিডন স্ট্রিট ও নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড, উত্তরে শ্যামবাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট"। বটতলার আশেপাশের গলিগুলো সাধারণভাবে 'বটতলা' নামেই পরিচিত ছিল এবং এসব থেকে যে সব বই প্রকাশিত হত, তা হীনার্থে 'বটতলার পুঁথি' নামে খ্যাত ছিল। সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পুঁথি, পাঁচালি, পঞ্জিকা, পুরাণ, লোককাহিনি ইত্যাদি এখান থেকে প্রকাশিত হত। লাভের কথা চিন্তা করে বটতলার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে এমন কিছু বই যার মূল উপজীব্য শহরের বহু নামী পরিবার কিংবা সমাজপতিদের পরিবারের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা। কারও-কারও মতে, 'কেচ্ছার বই' মানেই নাকি 'বটতলা সাহিত্য'। বটতলায় ছাপা পঞ্জিকা সেই আমলে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঝাঁকায় করে বিক্রি করত ফেরিওয়ালারা। আর সেই পঞ্জিকার ফাঁকেই অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ে তখনকার নানা কেচ্ছা কাহিনি। বটতলা যে কেবল নিম্নমানের গ্রন্থই প্রকাশ করেছে তা নয়; তা দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রযুক্তির উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান রেখেছে। গ্রন্থে ছবি ও চিত্র সংযোজন এবং নানারকম অলঙ্করণ বটতলারই অবদান।
শিক্ষিত ভদ্রলোকরা বটতলা সাহিত্যকে নিচু চোখে দেখত, কারণ তার ভাষা ছিল পর্ণগ্রাফি ঘেঁষা, যদিও তা এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সমাজেতিহাসের পাঠ। অথচ এই সব সাহিত্য আমরা সংরক্ষণ করিনি, করার যোগ্য বলে মনে করিনি, অশ্লীল বলে, তাই অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। উনিশ শতকের কাউন্টারকালচার সাহিত্যের লেখকরা হলেন টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের টেক্সটগুলো রয়ে গেছে কারণ এঁরা ছিলেন উচ্চবর্ণের, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।
।। ১১ ।।
পাদ্রি জেমস লং, যিনি 'নীলদর্পণ' (দীনবন্ধু মিত্র) ইংরেজিতে অনুবাদ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং সেই কারণে জেলে গেলেন, তিনি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কে বলেছিলেন ইতরদের সাহিত্য। দাশরথি রায় ও অন্যান্য পাঁচালিকারদের পাঁচালিগুলোকে বলেছিলেন মোটা দাগের লালসাউদ্রেককারী কাজ। বাঙালিদের উচিত মিল্টন, চসার ইত্যাদি ব্রিটিশ কবিদের কবিতা পড়া। এরপরই বাঙালির বৌদ্ধিক জীবন থেকে বিতাড়িত হলেন ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য পাঁচালিকাররা।
।। ১২।।
এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যাবাসী হলেও গোপাল উড়ের কথা বলতে হয়। গোপাল উড়ে উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুর গ্রামের এক চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুকুন্দ করণ। জীবিকার জন্য তিনি কলকাতা আসেন ও ফল ফেরি করার ব্যবসা শুরু করেন। 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাদলের কর্ণধার বিশ্বনাথ মতিলাল গোপালের উচ্চস্বরে ফল বিক্রয়ের হাঁক শুনে তাঁকে ডেকে আনেন। এরপর যাত্রাদলে ভর্তি করে নেন। সেখানে হরিকিষণ মিশ্রের কাছে গানের তালিম পান তিনি। নিজ প্রতিভাগুণে তিনি এই যাত্রাদলের অভিনেতা এবং গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এরপর ভাল করে বাংলা ভাষা শিখে মঞ্চে নামার অধিকার লাভ করেন। এই সময় রাধারমন সরকারের নেতৃত্বে যাত্রাগানের আসর বসে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে, সেখানে গোপাল উড়ে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় ও গান করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। রাধারমন সরকারের মৃত্যুর পর এই যাত্রাদল ভেঙে যায়। এরপর গোপাল নতুন আঙ্গিকে একটি যাত্রাপালার দল করেন। এই দলের সূত্রে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, প্রভূত যশ এবং সম্পদের অধিকারী হন। উড়িষ্যাবাসী বলে তার দল গোপাল উড়ের যাত্রাদল নামে পরিচিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গোপাল উড়ের উল্লেখ আছে।
।। ১৩ ।।
চারণকবি মুকুন্দদাসের (১৮৭৮ - ১৯৩৪) কথাও বলতে হবে। মুকুন্দদাসের বাবার মুদির দোকান ছিল বরিশালে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, কীর্তন গাইতেন। মুকুন্দদাস ক্লাস এইটে স্কুল ছেড়ে দেন। মাস্টারমশাই স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তর প্রভাবে 'মাতৃপূজা' নামে দেশাত্মবোধক পালাগান লিখে বাংলার গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই পালাগান। 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর' বা 'সন্ধ্যা'র মতো বিপ্লবী পত্রিকাগুলো মুকুন্দদাসের পালা সম্পর্কে লিখে তাঁকে আরও জনপ্রিয় করেছিল। ব্রিটিশ শাসক তাঁকে ৩ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল।
।। ১৪ ।।
লালন ফকির ( - ১৮৯০) সমাজের মূলস্রোতের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন এক কাউন্টারকালচার জীবনযাপনের সমাজ, লিখেছিলেন কাউন্টারকালচার জীবনবোধের গান, প্রচার করেছিলেন জাতপাত সমাজশাসিতযৌনতাবিরোধী এক নতুন মানব ধর্ম। যাঁর রচিত অন্তত ৬০০ গান বাংলার ফকিররা গেয়ে আসছেন গত দেড়শো বছর ধরে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন বা লেখক মীর মোশারফ হোসেনের মতো অভিজাত বিদ্বজনরা লালনের কথা জানলেও তাঁর জীবনী লিখে রাখার কথা ভাবেননি, কারণ লালন ও তাঁর চর্চিত জীবন ও সঙ্গীতকে নিচু সমাজের নোংরা ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন তাঁরা।
(সমাপ্ত)
চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।