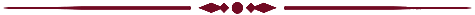
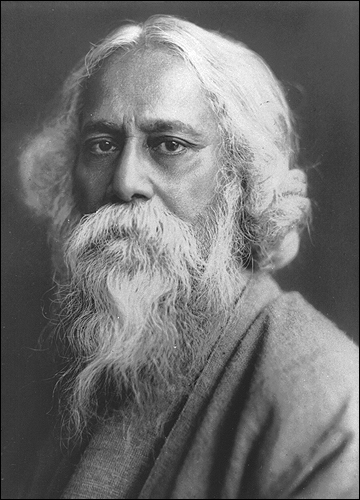
রবীন্দ্রচেতনায় যে উদার মানবিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায় তার পিছনে ছিল তাঁদের পারিবারিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই সংস্কৃতি মিশ্র চরিত্রের। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতার চর্চা, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ধর্মীয় চেতনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আত্ম-চেতনার সূচনা ও বিকাশ লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তা ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বৈশিষ্ট্যেও। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য, রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কার এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা ও সাহিত্য সৃষ্টি। সেই সঙ্গে ভিন্ন ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখের সাহিত্যকর্ম, বিপরীত ধারায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হিন্দুত্ববাদী স্বাদেশিকতা ওই সমাজের রক্ষণশীল ঘরানায় ব্যাপকভাবে, গভীর আবেগে সমাদৃত হয়েছিল। এভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধর্মীয় চেতনা এবং সাহিত্য ও বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছিল। এক কথায় বলতে গেলে পারিবারিক পরিবেশ রবীন্দ্র চেতনায় উদার মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বদেশে সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রভাব। তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং সেখানকার উদার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ মিলেছিল। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটেছে।
আশি বছরের দীর্ঘ জীবন অবিবাহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। নানা উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধ সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজের মতো করে শিক্ষা নিয়েছেন, নিজের চেতনা ও বোধের পরিধিকে প্রসারিত করেছেন। তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন এবং নিজের বোধ অনুযায়ী সমাধানের উপায় ও পথ সন্ধান করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগে কারও সমর্থন আসুক বা না আসুক, তিনি নিজের অবস্থান বা যুক্তিতে অনড় থেকেছেন। সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করেছে তা হলো হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়গত সম্পর্কের অনাকাঙ্ক্ষিত দিক। এ বিষয় নিয়ে জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত ভেবেছেন এবং সমস্যার সমাধানের উপায় বের করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এ নিয়ে তিনি বিভিন্ন লেখায়, চিঠিপত্রে এবং ভাষণে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪) শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।" এখানে 'পাপ' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে রাখঢাক না করে তাঁর উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে:
"আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।" এই 'বিরুদ্ধ' সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করে লিখেছেন:
"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।"
তিনি আরও লিখেছেন, "আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না — ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।"
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ একথা উল্লেখ করেছেন। এই 'জাজিম তোলা'র অভিজ্ঞতা হয় শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনা করতে এসে। সে প্রসঙ্গ পরে উল্লেখিত হবে। এই 'জাজিম তোলা'র শাস্ত্রীয় বিধানের অজুহাত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:
"তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখিনা। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।"
ভেদ প্রথার অবসান
জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিভেদকে রবীন্দ্রনাথ সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন মানবতাবাদী হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁর জন্ম হয়েছিল বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কিছুটা হলেও বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা। এর প্রভাব প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপর থাকলেও সমাজ ও কালের বিবর্তনে তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে ১৮৯০-৯১ সালে পারিবারিক জমিদারি পরিদর্শন সূত্রে নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় তাঁর। এর মধ্য দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পেশাগত দিক থেকে তো নয়ই, কোনো দিক থেকেই এরা অপমানিত হতে পারেন না। ১৮৮৪ সালে 'ধর্ম' সম্পর্কে একটি আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন:
"জগৎ কাহাকেও এক ঘরে করে না, ধোপা-নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র, সূর্য, রোদ, বৃষ্টি জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশ সমগ্রের দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে।"
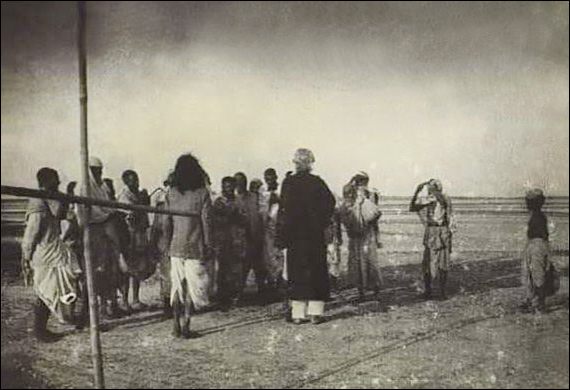
শিলাইদহে দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের জমিদারি আমলে নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় মুসলমান প্রজাদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। হিন্দুদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক (মাত্র ১০ শতাংশ) ছিলেন উচ্চবর্ণের, বাকি বিপুল সংখ্যক ছিলেন নিম্নবর্ণের অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণির। জমিদারি তদারকি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে জনসমাজের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক সম্পর্কের চরম অবনতি প্রত্যক্ষ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন:
"অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।"
(হিন্দু-মুসলমান, কালান্তর)

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি।
প্রসঙ্গক্রমে এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব পাবার পর ১৮৯১ সালে প্রথম শিলাইদহে এলেন পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে। এসে প্রথমেই যে প্রায় বৈপ্লবিক কাজটি করলেন তা হলো আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে জাতি ও বর্ণভেদ ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দিলেন। ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর-এর আমল থেকেই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে সম্ভ্রম-মর্যাদা ও জাতি-বর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা ছিল। প্রথাগত নিয়ম অনুসারে হিন্দুরা বসতেন চাদর ঢাকা শতরঞ্চির উপর এক পাশে, আর তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল আলাদা আসন।আর মুসলমান প্রজারা বসতেন চাদর ছাড়া শতরঞ্চির উপর অন্য ধারে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা আসনে বসতেন। জমিদার অর্থাৎ বাবুমশাইয়ের জন্য ছিল ভেলভেট মোড়া সিংহাসন।
রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে এসে এই ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করলেন। তিনি জাত-বর্ণ অনুসারে আসনের এই বিভাজন প্রথা তুলে দিতে বললেন। এ নিয়ে নায়েব-গোমস্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মতবিরোধ হলো। এমনকী তাঁরা একযোগে পদত্যাগেরও হুমকি দিলেন। তাঁদের বক্তব্য, চিরাচরিত প্রথা ভাঙা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবস্থানে অবিচল রইলেন। তিনি বললেন, মিলন উৎসবে পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে মধুর সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। তিনি প্রজাদের নির্দেশ দিলেন পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা সব সরিয়ে দিয়ে সবাইকে একসঙ্গে বসতে। তাঁর আহ্বান অনুযায়ী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আসনের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে ঢালা ফরাশের উপর বসে পড়লেন। আর সিংহাসনের পরিবর্তে সবার মাঝখানে বসলেন তাদের 'বাবুমশাই' ― রবীন্দ্রনাথ। দলে দলে এলেন আরও লোক। সেদিন থেকেই ঠাকুরদের জমিদারিতে পুণ্যাহ উৎসবে শ্রেণিভেদ প্রথা উঠে গেল।
কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক ভাষণ নতুন সমস্যা-সংঘাতেরও জন্ম দিল। দরিদ্র প্রজারা তাদের দুঃখ যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হবার সম্ভাবনা অনুভব করলেন, অন্যদিকে আমলা এবং সম্পন্ন মহাজনেরা টের পেয়ে গেলেন যে, তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখা আগামী দিনে কঠিন। এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের দিনই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, "সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।" এখানে 'সাহা' বলতে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝাতে চান নি,' শেখ' বলতেও তা নয়। তাঁর জমিদারিতে অধিকাংশ মহাজনই ছিলেন সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু, সেজন্যই মহাজন অর্থে তিনি 'সাহা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাঁর জমিদারিতে বেশিরভাগ দরিদ্র প্রজাই ছিলেন মুসলমান। তাই 'শেখ' অর্থে দরিদ্র প্রজাদেরই বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে প্রথম থেকেই কায়েমি স্বার্থের যে সমস্ত জায়গায় আঘাত হেনেছিলেন, তার সবক'টিরই রক্ষক ছিলেন হয় হিন্দু গোমস্তা, নয় হিন্দু মহাজন বা জোতদার। সেই প্রথম তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়চেতা মনোভাব আর জনকল্যাণের উদ্যোগে বিপন্ন বোধ করলেন। তাই তাঁদেরই একাংশ স্বার্থের তাগিদেই নানা ছলে বিরোধিতায় মত্ত হয়েছিলেন। আবার ঠাকুরদের জমিদারির অধিকাংশ প্রজাই যেহেতু ছিলেন দরিদ্র মুসলমান, তাই কল্যাণকর্মে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছিলেন ওই মুসলমান প্রজারাই। তাই তাঁদের ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও আস্থা। এমনও জানা যায় যে, কিছু স্বার্থান্বেষী লোক গ্রামের উন্নয়নের কথা ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে বয়ে এনেছিলেন জমিদারিতে। এমনও কথা উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, তাই তাঁর এত মুসলমান-প্রীতি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রজা-পীড়ক ছিলেন — এমন সবৈব মিথ্যা প্রচার হয়েছে বলেও জানা যায়।
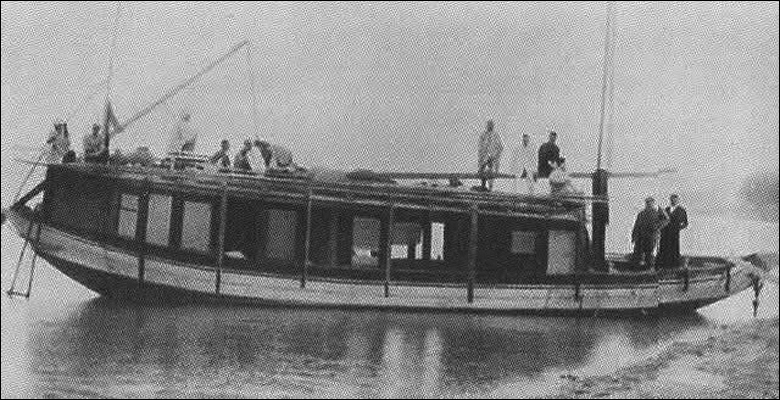
পদ্মা নদীতে বজরায় রবীন্দ্রনাথ।
এই সূত্রেই এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার মধ্য দিয়ে বর্ণ-সম্প্রদায় বা জাতিভেদের বিপরীত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিপন্থী এক চিরন্তন অনাবিল মানব প্রেমের ভিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে প্রোথিত ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই মহৎ ভাবনাকেই তিনি তাঁর জমিদারির কাজ পরিচালনার সময়ে সমস্ত কল্যাণকর্মের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শাহজাদপুরে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অসামান্য কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। যা তুলে ধরেছেন ড. মজহারুল ইসলাম তাঁর 'শাহজাদপুরে জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাফল্য' প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য: দেশ, ২৫ চৈত্র ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১৯-২৫)। ঘটনাটি এরকম ড. ইসলামের পিতামহ নবীপুরের আকুল সরকার ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাউল ভদ্রের কন্যা লতা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোপনে বিয়ে করেন। বাউল ভদ্র ছিলেন মুড়াপাড়ার ব্যানার্জি জমিদারের প্রজা। তিনি জমিদারের কাছে অভিযোগ করেন যে, আকুল সরকার জোর করে তাঁর কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেছে। জমিদার ও তাঁর ম্যানেজার আকুল সরকারকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন, অন্যদিকে আকুল সরকারও তাদের বাধা দিতে প্রস্তুতি শুরু করেন। এ নিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হয়। রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুরে এসেই আকুল সরকার ও লতার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই মতো রবীন্দ্রনাথ সিরাজগঞ্জের তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট এফ ও বেল শাহজাদপুর এলে এই বিষয়টি জানান এবং দু'জনের প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনা দূর হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে আলোচনার কথা উল্লেখ করে আকুল সরকারকে লেখেন, "তুমি নিজের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করোনি, এইটে আমার ভালো লেগেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের নিকট মানুষের মর্যাদার বাড়া আর কিছু নেই। নারী-পুরুষের প্রেমও এই শাসনই মেনে চলে — সে হৃদয়ের বশ, ধর্মের বা বর্ণের অনুশাসন তার বড়ো নয়। সমাজ প্রাচীর গড়ে কিন্তু হৃদয় অনায়াসেই সেই প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে। তোমাদের সাথে আলাপ করে আমি তেমন দুটো হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছি। শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শাসনকে নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করো না। আশা করি তোমাদের যে অত্যাচারের আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা দূরীভূত হয়েছে। তোমরা আমার সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদাই লাভ করবে। সুখী হও। শুভার্থী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"
'মানুষের ধর্ম'
রবীন্দ্রনাথ কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বা তাঁর ধর্ম-চিন্তা কী ছিল ইত্যাদির উত্তর সন্ধানে অথবা উপসংহারে পৌঁছাতে হলে আমরা দেখি তাঁর ধর্ম-চিন্তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের গভীর উপলব্ধি, মানসিক দ্বন্দ্ব বিরোধ এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ পরিক্রমা করে তিনি যে ধর্ম-চিন্তায় উপনীত হয়েছিলেন তা হলো 'মানুষের ধর্ম'। তিনি ছিলেন প্রধানত উদার মানবতাবাদী, যিনি মনুষ্যত্বকে মানবধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এই ধর্ম মানুষকে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। মানুষকে মানুষের সাথে ঐক্যের সূত্রে গেঁথে দেয়। মানুষের ধর্মের মধ্যে মনুষ্যত্বতার সমস্ত গুণাবলি নিয়ে সজীব থাকে। মানবমিলনই হয় তার অভিমুখ। 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' শীর্ষক বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন মানুষের ধর্মই পারে মানুষকে 'অপরাজিত মানুষ' আখ্যালাভে প্রেরণা দিতে। প্রাতিষ্ঠানিক যে ধর্ম রবীন্দ্রনাথের কথায় যা 'সাম্প্রদায়িক ধর্ম' যাকে তিনি কখনো বলেছেন 'ধর্মতন্ত্র'। এর মূল উৎস মানুষের অসহায়তাবোধ, দুঃখ, বিপন্নতা, রোগ-জরা, মৃত্যুজনিত ভয় এবং দুর্বলতা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মকে আত্মস্থ করে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চান তা মূলত ব্যক্তিগত ও যৌথ জীবনযাপনের এক অতি উন্নত আদর্শ। অর্থাৎ জীবনের ইতিবাচক ও অনুকূল দিকগুলিকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করব, কোন বস্তু, বিশ্বাস, আদর্শ গ্রহণ বা বর্জন করব; অন্য মানুষ প্রাণী এবং বিশ্ব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে — এই ধর্ম তার যুক্তিসংগত ও মানবিক নির্দেশ দেবে।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ব্যক্তি জীবনে ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও রবীন্দ্রনাথ সব রকম ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, অসম্প্রীতির বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। তিনি 'ধর্মমোহ' ('পরিশেষ', ১৯৩২) কবিতায় উচ্চারণ করেছেন:
"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।"
এই সময়ে ভারতের মতো দেশে (প্রতিবেশী বাংলাদেশেও) উগ্র ধর্মান্ধতার অভিঘাতে এক অস্থির বিকারগ্রস্ত পরিবেশে এই কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলাই বাহুল্য।
ঈশ্বরের নামে ভণ্ডামি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে
ঈশ্বরের নামে এবং অসহায় বিপন্ন মানুষদের দুর্বলতার সুযোগে একশ্রেণির গুরুদেব, মহান্ত, পাদরি ও পুরোহিত নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে চূড়ান্ত ভণ্ডামির মাধ্যমে মানুষকে নিংড়ে যেভাবে প্রতারণা ও শোষণ করে তার বাস্তব চিত্র আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও চিঠিপত্রে। তেমনি একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে ১৯৩১ সালের ১৭ জুন তারিখে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে —
"গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেম তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রাণী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন — ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে, অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য সময়প্রীতি ভক্তি সমস্ত দিচ্ছে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগ্য মানুষের প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে।"...
আবার ধর্মমোহে, ধার্মিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ যে কতভাবে অপমানিত, বিপর্যস্ত ও বঞ্চিত হয় রবীন্দ্রনাথ তারও স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ১৩৩৭ সালের ২৯ চৈত্র হেমন্তবালা দেবীকে আরেকটি চিঠিতে তিনি মানসিক ক্ষোভ ব্যক্ত করে লিখছেন:
"মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে। খেলার দেবতা এইসব সোনা জহরৎকে ব্যর্থ করে বসে থাকুন — এদিকে সত্যকার দেবতা সত্যকার মানুষের কঙ্কালশীর্ণ হাতের মুষ্টি প্রসারিত করে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরছেন... আমি মানুষকে ভালোবসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া।"...
কবির এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রতীক পুজো, সাধনভজন ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ অপব্যয়ের চেয়ে দরিদ্র নিরন্ন হতভাগ্য মানুষদের তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মানুষকেই দেবতার আসনে বসিয়েছেন। তথাকথিত ধর্মীয় আবেগ ও ভাবময়তার চেয়ে যুক্তিবুদ্ধি বিজ্ঞান ইত্যাদি যে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাও স্পষ্ট হয়েছে। তাই ধার্মিকের চেয়ে কর্মোদ্যোগী নাস্তিকের সমাদর করতে তিনি আগ্রহী। তিনি লিখেছেন:
"কত লোক দেখেচি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে, আবার এও প্রায়ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্মিক বলেই মনে করে তারা সর্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে বঞ্চিত করে।"... (পূর্বোক্ত, ৮ আষাঢ়, ১৩৩৮/ইং- ২৩ জুন, ১৯৩১)
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (১৪ জুন, ১৯৩১) রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে অকপটেই উল্লেখ করেছেন:
"আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয় — আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে — সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে — যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেচেন, সেইখানে নারীর পূজা সত্য হয়েচে।... যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না।"
রবীন্দ্রনাথ জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনন্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে ভাবলোক থেকে মর্ত্যধূলির 'পরে পদচারণা করে মানবলোকে উপনীত হয়েছেন। তিনি মানুষকেই তাঁর দেবতার আসনে বসিয়েছেন। দৃঢ়চিত্তে তিনি উচ্চারণ করেছেন: "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" (সভ্যতার সংকট)। তিনি ভারতে-বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষায় আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যেমন ছিল, তেমনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে ব্যক্তিগত প্রয়াস প্রতি মুহূর্তে জারি রেখেছেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি লিখেছেন:
"আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা।... বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশী সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।" ('হিন্দু-মুসলমান', সাধনা, ১৩৩১)।
রবীন্দ্রনাথ ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে বহুর মধ্যে এক-এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে যে চিন্তা এবং স্বপ্নকে তিনি মনের গভীরে লালন করেছেন, সেটাই মূর্ত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন:
"যদি ভারতীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।... হিন্দু-মুসলমান ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে...। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দু-মুসলমানের বেশ।" ( 'ভারতী', ১৩০৫)
কবির এই উদার মানবিক আদর্শ আজ আমাদের দেশে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। পরাধীনতার গ্লানি মোচনে এবং বিপন্ন মানব সভ্যতার ত্রাতার ভূমিকায় বারে বারে রাজপথে নেমে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামের বাণী উচ্চকিত করেছেন। অথচ তাঁর এই 'দুর্ভাগা দেশে' উগ্র ধর্মান্ধদের শাসনে দুর্ভর অন্ধকারের কালোছায়া ক্রমশ প্রলম্বিত হচ্ছে।
অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, হিংসা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে এই হিংসাশ্রয়ী দুর্বৃত্তরা দেশ ও সমাজের প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনছে। এই বিপদ আজ নানাভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দেখা দিয়েছে। বিশেষকরে প্রতিবেশী বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের প্রচ্ছন্ন মদতে উগ্র মৌলবাদী শক্তির উন্মত্ত আস্ফালন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ যাবতীয় শুভবোধ, প্রগতিচেতনা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দেশে পশ্চাৎমুখী চরম অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে। এই অপহ্নবকালে সেখানে মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের বিশ্বকবির মূর্তি ভাঙা ও প্রতিকৃতি কালিমালিপ্ত করার মতো জঘন্য অপরাধ করতেও দেখা যাচ্ছে। তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরও ধ্বনিত হচ্ছে নানা দিকে। এই ঘনঘোর কালো অশান্ত প্রতিবেশে তীক্ষ্ণ আয়ুধের মতো আমাদের সামনে ভেসে আসে রবীন্দ্রনাথেরই অমোঘ আহ্বান —
"যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।" ('ধর্মমোহ')
প্রাসঙ্গিক তথ্য:
১) রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিভিন্ন সংখ্যা।
২) জমিদার রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭।
৩) রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯।
৪) প্রসঙ্গ: অনন্য রবীন্দ্রনাথ - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, সার্ধ-শততম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্যাপন সমিতি, নবযুগ প্রকাশন, গুয়াহাটি-৭৮১০০৩।
৫) রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা-দেবলোক থেকে মানবলোক, সম্পাদনা বিজয় পাল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি, মেদিনীপুর-৭২১১০১।
৬) রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ও কাব্যে আধুনিকতা, আহমদ রফিক, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।

লেখক: সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক।